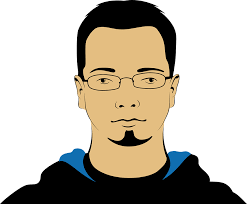


রাজনীতিক প্রভাব ও রাষ্ট্রযন্ত্রের দখল— নির্বাচনীয় নিরপেক্ষতার পথে সবচেয়ে বড় বাধা” কথাটা শুনতে অন্যরকম। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই বাস্তব।
বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে আবারও প্রশ্ন উঠেছে— রাজনৈতিক অস্থিরতার এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কতটা নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হবে?
বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশের অঙ্গন এখন এক সংকটময় দ্বিধার মধ্যে দাঁড়িয়ে। একদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্বাচনকালীন প্রস্তুতি, অন্যদিকে বিরোধী দলের দাবিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রত্যাবর্তন— এই দুইয়ের টানাপোড়েনে জাতি এক অনিশ্চিত দিকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে আবারও প্রশ্ন উঠেছে— রাজনৈতিক অস্থিরতার এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কতটা নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হবে ?বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন এখন এক সংকটময় দ্বিধার মধ্যে দাঁড়িয়ে। দেশজুড়ে চলমান আন্দোলন, পাল্টা কর্মসূচি, এবং প্রশাসনিক পক্ষপাতের অভিযোগের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী পরিবেশ ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিরোধী দলগুলো বলছে, সরকারের অধীনে নির্বাচন মানেই “পূর্বনির্ধারিত ফলাফল”, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন অন্তবর্তী কালীন সরকার দাবি করছে, জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচনই হবে এবং তা হবে “সুষ্ঠু ও অংশ গ্রহণমূলক। শতভাগ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন নির্বাচন কমিশন। এখন প্রশ্ন নির্বাচন কি হবে তত্ত্ববোধক সরকারের অধীনে? না সরকারের অধীনে। সে যাই হোক, একদিকে সরকারের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা, অন্যদিকে বিরোধী দলগুলোর দৃঢ় অবস্থান— “ফ্যাসিবাদী দোসরদের হাতে ক্ষমতা রেখে কোনো নির্বাচনই নিরপেক্ষ হতে পারে না। আর ফ্যাসিবাদ মুক্ত করতে যে সময় এর প্রয়োজন সে সময় সরকারের হাতে নেই। যে কারণে বিএনপি নেতৃবৃন্দসহ বিরোধী রাজনৈতিক জোটগুলো বলছে, বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো কার্যত দলনির্ভর এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সক্ষমতা রাখে না। তাদের মতে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক কাঠামোয় রূপান্তরিত হতে হবে— যাতে সব রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন করা যায় এবং নির্বাচন কমিশন সত্যিকার অর্থে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।
বিএনপি মহাসচিব সাম্প্রতিক এক বক্তব্যে বলেন, “দেশে আজ ভয়, দমননীতি ও রক্তের রাজনীতি চলছে। বর্তমানে প্রতিনিয়ত নদীতে মানুষের ভাসমান লাশ খুঁজে পায়, ঘরে ঢুকে হত্যা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের অধীনে নির্বাচন মানে প্রহসন। জামাতের আমির এখনো বলে যাচ্ছেন পিয়ার পদ্ধতি ও গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচন হতে হবে। এনসিপির নেতৃবৃন্দরা বলছেন, জামাত ফ্যাসিবাদীদের পূর্ণবাসন করার চেষ্টা করছে। এখন প্রশ্ন জনগণ কোনটা ভেবে নিবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও বলছেন, ফ্যাসিবাদী প্রবণতা যদি প্রশাসনের ভেতরে থেকেই যায়, তাহলে নির্বাচন কমিশন যতই নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করুক, নির্বাচনী পরিবেশ স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য হবে না। এছাড়াও বিশেষজ্ঞজনের অভিমত নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করতে হলে আগে নির্বাচনীয় পরিবেশ ঠিক করতে হবে। কোন বিষয়ে দলীয়করণ করা যাবে না একেবারে নিরপেক্ষ হতে হবে। আগামী নির্বাচনে যেহেতু পেশী শক্তির ব্যবহারের সম্ভাবনা
বেশি রয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে হয়তো সেটা বিস্তার লাভ করতে পারে।
সরকার দাবি করছে, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন নির্ধারিত সময়েই হবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রশাসনিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু জনমনে প্রশ্ন— এই সরকার যদি একই রাজনৈতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে সেটি কি সত্যিই “নিরপেক্ষ”?
দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও রাজনৈতিক স্থিতি ফিরিয়ে আনতে এখন একটাই পথ— এমন একটি অন্তর্বর্তী কাঠামো গঠন করা যা দলীয় প্রভাবমুক্ত ও জনগণের আস্থার প্রতীক হতে পরে।নির্বাচন কেবল ভোটের দিনেই হয় না— এটি বিশ্বাসের ওপর দাঁড়ানো এক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।
যদি সেই বিশ্বাস ফ্যাসিবাদের ছায়ায় ঢাকা পড়ে, তবে ব্যালট যতই স্বচ্ছ হোক, জনগণের আস্থা আর ফিরে আসে না।
নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নির্ভর করে মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর— প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা,ও রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক আস্থা। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই তিনটি ক্ষেত্রেই প্রশ্ন উঠছে। প্রশাসনের নিয়োগ, পুলিশি অভিযান, এবং বিরোধী দলের সভা-সমাবেশে বাধা— এসব ঘটনাই নির্বাচনী আস্থাকে দুর্বল করছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া টিকিয়ে রাখতে হলে নির্বাচন হতে হবে অংশগ্রহণমূলক, প্রতিযোগিতামূলক ও আস্থাভিত্তিক। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা এবং পক্ষপাতমূলক প্রশাসনিক আচরণ সেই আস্থার ভিত্তি নষ্ট করছে। তারা মনে করেন, একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গঠনই হতে পারে আস্থার পুনরুদ্ধারের পথ। এতে সরকার পরিবর্তন না হলেও নির্বাচনকালীন দায়িত্ব থাকবে দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের হাতে, যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া হয় স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম জরিপে দেখা গেছে, জনগণের বড় একটি অংশ এখনো বিশ্বাস করে— তত্ত্বাবধায়ক বা নিরপেক্ষ কাঠামো ছাড়া নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। এমন প্রেক্ষাপটে দেশের মানুষ একটি শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচনের প্রত্যাশা করা।
“নির্বাচনের নিরপেক্ষতা কোনো আইনি কাঠামোর ফল নয়; এটি জনগণের বিশ্বাসের প্রতিফলন। যেখানে আস্থা অনুপস্থিত, সেখানে গণতন্ত্র কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সরকারের মধ্যে শব্দোত্তরগুলো নিরপেক্ষতা। আশা করি বিষয়টি সরকার ও নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ বিশেষ ভাবে বিবেচনা করবেন না। যাতে আগামী অভাব নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র বাস্তবে উপায়। ২০২৫ সালের অক্টোবর নাগাদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে। রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলায় আন্দোলন, অবরোধ, সংঘর্ষ এবং গ্রেফতার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সরকার ঘোষণা দিয়েছে— সংবিধান অনুযায়ী আগামী ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু বিরোধী দলগুলো বলছে, “বর্তমান ক্ষমতাসীন শক্তির হাতে নির্বাচন মানেই পূর্বনির্ধারিত ফলাফল।অন্তবর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, “জুলাই সনদ”-এর আলোকে নির্বাচন হবে সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শতভাগ নিরপেক্ষ। নির্বাচন কমিশনও আশ্বাস দিয়েছে— প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের।কিন্তু জনমনে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে— এই সরকার যদি একই রাজনৈতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে সেটি কি সত্যিই “নিরপেক্ষ”?বিএনপি নেতৃবৃন্দসহ বিরোধী রাজনৈতিক জোটগুলোর দাবি— বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো কার্যত দলনির্ভর, এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের মতে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক কাঠামোয় রূপান্তরিত হতে হবে, যাতে সব রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন করা যায় এবং নির্বাচন কমিশন সত্যিকার অর্থে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলেন, “দেশে আজ ভয়, দমননীতি ও রক্তের রাজনীতি চলছে। নদীতে মানুষের লাশ ভাসছে, ঘরে ঢুকে মানুষ হত্যা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকারকে আরো সতর্ক হতে হবে। অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামী এখনো বলছে, গণভোট বা পিয়ার পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন হতে হবে, যাতে জনগণ সরাসরি রায় দিতে পারে।
অন্যদিকে এনসিপি (ন্যাশনাল কনজারভেটিভ পার্টি)-এর নেতারা মনে করেন, জামায়াত ও কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী আসলে “ফ্যাসিবাদীদের পুনর্বাসন” করার চেষ্টা করছে।
এই দ্বিমুখী অবস্থানের ফলে জনমনে বিভ্রান্তি ও অনাস্থা আরও গভীর হচ্ছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ফ্যাসিবাদী প্রবণতা যদি প্রশাসনের ভেতরে থেকেই যায়, তাহলে নির্বাচন কমিশন যতই নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করুক, নির্বাচনী পরিবেশ স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য হবে না। যে বিষয়গুলো স্পর্শকাতর সে বিষয়গুলো এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ক্ষেত্রেই ঘাটতি স্পষ্ট।
পুলিশি অভিযান, বিরোধী সভা-সমাবেশে বাধা, এবং সরকারি কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা— এসবই নির্বাচনী আস্থাকে দুর্বল করছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন,“নির্বাচনের নিরপেক্ষতা শুধু আইনি কাঠামোর ব্যাপার নয়; এটি জনআস্থার ফল। যেখানে মানুষ বিশ্বাস হারায়, সেখানে ব্যালট আর গণতন্ত্রের প্রতীক থাকে না— সেটি হয়ে ওঠে আনুষ্ঠানিকতা
সাম্প্রতিক কয়েকটি গণমাধ্যম জরিপে দেখা গেছে, দেশের প্রায় ৬২% ভোটার মনে করেন— তত্ত্বাবধায়ক বা নিরপেক্ষ কাঠামো ছাড়া নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। প্রায় ৭০% নাগরিক মনে করেন, নির্বাচনের আগে সহিংসতা ও প্রশাসনিক পক্ষপাত রোধে স্পষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হলে, রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও দীর্ঘায়িত হবে— এমন আশঙ্কাও করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।
সরকার দাবি করছে, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন নির্ধারিত সময়েই হবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রশাসনিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে। তবে রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া নির্বাচনী পরিবেশ স্থিতিশীল হবে না— এমনটাই বলছেন দেশি-বিদেশি কূটনীতিকরা।
তারা মনে করছেন, সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের মধ্যে “ন্যূনতম আস্থার সেতু” তৈরি করতে না পারলে সহিংসতার আশঙ্কা থেকেই যাবে।
বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখন আস্থার এক সঙ্কটকাল অতিক্রম করছে।অতএব, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও রাজনৈতিক স্থিতি ফিরিয়ে আনতে এখন একটাই পথ। এমন একটি অন্তর্বর্তী কাঠামো গঠন করা যা দলীয় প্রভাবমুক্ত, প্রশাসনিকভাবে স্বাধীন এবং জনগণের আস্থার প্রতীক হতে পারে।
লেখক ও গবেষক:
আওরঙ্গজেব কামাল
সভাপতি
ঢাকা প্রেসক্লাব।